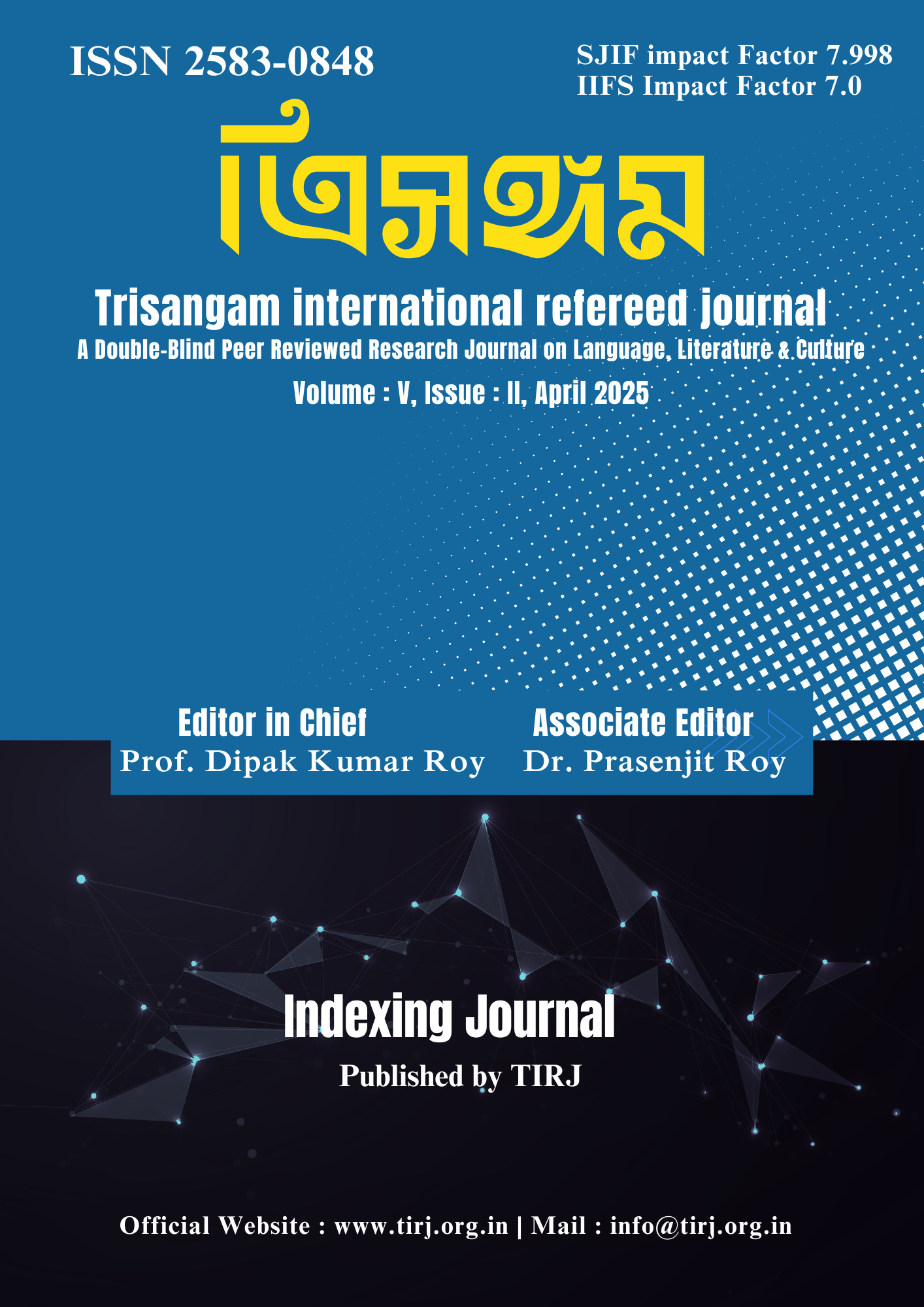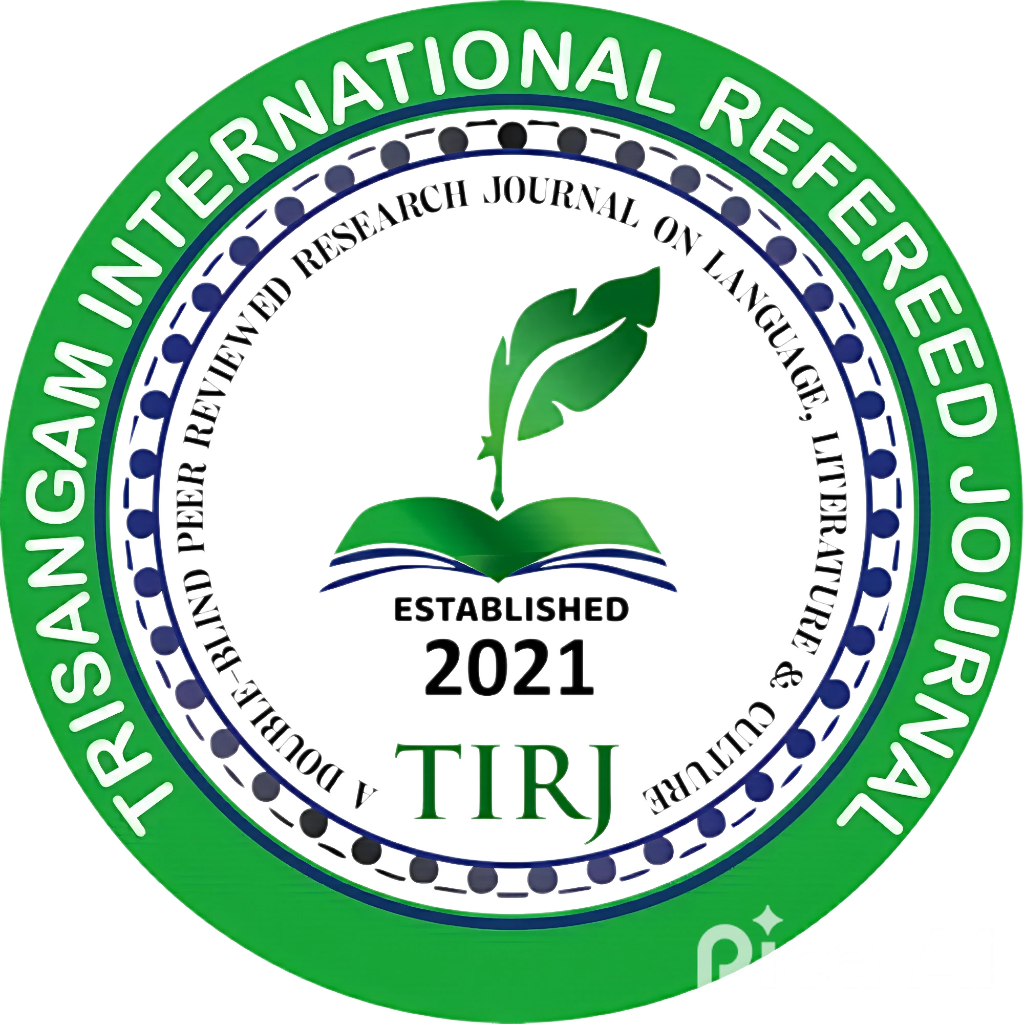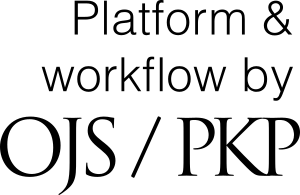The conflict between the religion of conduct and the religion of the heart: Rabindranath's 'Malini'/ আচার ধর্ম ও হৃদয় ধর্মের দ্বন্দ্ব : রবীন্দ্রনাথের ‘মালিনী’
Keywords:
- Brahma Dharma,
- Buddhism,
- Poetic Drama,
- Buddhist Philosophy
Abstract
Although the propagation and spread of Buddhism have changed in the present day, many were initiated into this religion in ancient times. Due to various conflicts, people were attracted to Brahma Dharma, and Buddhism began to decline rapidly. Although the practice of Buddhist thoughtwas revived in Bengal in the 19th century, it is still going strong even now. Maharishi Debendranath Tagore, Brahmananda Keshavachandra and their followers did not ignore the philosophy and ideals of Buddhism. Satyendranath Tagore wrote a valuable book named 'Buddhism', and on the other hand, Rahul Sankrityayan wrote a book called 'Mahamanav Buddha' on the biography of Buddha. Rabindranath was also deeply moved by the ideology of Buddha. Therefore, he not only tried to re-expand Buddha's intellectual thoughts in a new context through various studies but also created many works.
The narrative of the Malini play is created by mixing the Malini episode of 'Mahabastu-Avdan' ('Malinya Bastu'-The Story of Malini) with this dream tale. The story of 'Malinya-Avdan' of Mahavastu-Avdan is very extensive. At the request of RajendraLalMitra, HaraprasadShastri (then a young man) abridged the entire 'Mahabastu-Avdan'. Based on this extensive anecdote, Rajendralal Mitra published "The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal."(Cal,1882). Rabindranath became familiar with Buddhist stories through this abridged version. As a result, Rabindranath composed the poetic drama 'Malini'.
Downloads
References
১. ঘোষ, ড. তারকনাথ, ভারতসংস্কৃতি পুরুষ রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৪
২. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, বৌদ্ধধর্ম, তৃতীয় মুদ্রণ, করুণা প্রকাশনী, ১৪০৫, কলকাতা, পৃ. ৯
(“বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমিতে তার মৃত্যু হলেও, আজও তা কোটি কোটি এসিয়াবাসীর ধর্ম। শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চিন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকে আজও বুদ্ধদেবের পূজা করে, ও নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলেই পরিচয় দেয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হয় সমুদ্রের, নয় হিমালয়ের অপর পারের দেশসকল থেকেই এ দেশের এই লুপ্ত ধর্মের শাস্ত্র গ্রন্থসকল উদ্ধার করেছেন, এবং তাঁদের বই পড়েই আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান লাভ করেছি।”)
৩. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, মহামানব বুদ্ধ (অনুবাদ: ভট্টাচার্য, অভিজিৎ), তৃতীয় মুদ্রণ, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৪২০, পৃ.৯০
(“বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় যে অসাধারণ জীবনাদর্শ রেখে গেছেন-তা আপামর জনসাধারণের জন্য কল্যাণপ্রদ হয়ে উঠেছে। তিনি যে আচরণগত, দর্শনগত বা তত্ত্বগত এবং স্থৈর্যগত শান্তি দেখিয়েছেন, তার দ্বারা জনমুক্তির ও শান্তির দুয়ার আগলমুক্ত হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসে স্বাধীনতার পর যে ‘পঞ্চশীল’ শব্দটি বিদেশনীতির ক্ষেত্রে এত প্রচলিত সেটিও বুদ্ধেরই কথিত। অবশ্য বুদ্ধ রাষ্ট্রের জন্যে নয়-ব্যক্তির জন্যে এটা অধিক ব্যবহার করেছিলেন।
বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য কখনও রাজনৈতিক আগ্রাসনকে মূল্য দেওয়া হয়নি। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধরা নিজের বিচারকেই শ্রেষ্ঠ মানতেন এবং সেটাকে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না।... ধর্মের ব্যাপারে বুদ্ধ এবং তাঁর অনুচরদের লক্ষ্য মানসিক শক্তির বিকাশের দিকে কেন্দ্রীভূত ছিল। এর জন্য তাঁরা গভীর অনুচিন্তন এবং যোগের সাহায্য নিয়েছিলেন দেবতার ব্যাপারেও বৌদ্ধরা সমধিক উদার ছিলেন।”)
৪. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা, প্রথম সংস্করণ, পারুল, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭-১৮
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মালিনী, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৮৯, পৃ. ৫-৬
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্র, রবীন্দ্র রচনাবলী (উৎসবের দিন, ত্রয়োদশ খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ৩৯৬-৯৭
(“বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে-বৎস যেমন গাভী-মাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো-শ্রেণীর স্বার্থ-প্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্যবশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—
মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।।
তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতসিদ্ধো।
এতং সতিং অধিটঠেযং ব্রহ্মমেতং বিহার মিধবাহু।।
মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে-ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।
এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে-আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না-এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।”)
৭. চৌধুরী, ড. বিনয়েন্দ্র নাথ, বৌদ্ধ সাহিত্য, (সম্পাদক: চৌধুরী, ড. সুকোমল), প্রথম প্রকাশ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ- মুখবন্ধ অংশ
(“গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত অজস্র বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম যেমন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ও বিবর্তিত হইয়াছে, তেমনি বৌদ্ধ সাহিত্য ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। খ্রিস্টপূর্ব যুগে পালি ত্রিপিটক ভারতবর্ষে সংকলিত হইলেও পরবর্তীকালে সিংহল (শ্রীলংকা), ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) থাইল্যান্ড ও কম্পোডিয়ায় শত শত পালি টীকাগ্রন্থ, অনুটীকা, সারগ্রন্থ, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি রচিত হইয়াছে।... সংস্কৃত ভাষায় যে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তিব্বতী ও চিনা ভাষায় অনূদিত ও সংরক্ষিত গ্রন্থাদির তালিকা হইতে যাহাদের মধ্যে বহু মূল সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।”)
৮. Mitra, Rajendra Lal, The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, p. 121
দ্র: জানা, ড. রাধারমণ, পালিভাষা সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১০৬-১০৭
(“A Pratyeka Buddha entered the city of Vārānasi for alms, but got nothing. A girl finding his alms-bowl empty, brought him home, and gave him a hearty meal. When he died a stūpa was erected on his remains, and the girl decorated the stūpa everyday with flowers and aromatics. She desired that she may be born with a garland of flowers in every one of her future existence; her desire was fulfilled. In her next existence she was born a Devakanyā with a garland of flowers round her neck. From heaven she descended on earth, and was born in the same way as Mālini, the daughter of Kriki, king of Vārānasi. Mālini invited lord Kāsyapa and his retinue, and entertained them with a sumptuous meal. The Brāhmans, numerous and influential at the court of her father, taking umbrage at her conduct, induced the king to order her banishment. Mālini humbly begged for a week's respite, which was granted. During those seven days, five hundred of her brothers, the ministers and officers of the Bhatta army, and the citizens were all converted to the Ᾱrya Dharma. The converts regarded Mālini as the saviour of their souls. Angry at the wicked machinations of the Brāhmans, they proceeded in a body to remonstrate with them. The Brāhmans took refuge with the king. They revoked the sentence of Mālini's banishment; but induced the king to send ten armed men to kill Kāsyapa, the roof of all their woes. These armed men were easily converted by the great sage. They next deputed a larger number of men, but with the same result. They saw that by sending armed men they only added to the already overwhelming number of the perverts. They, therefore, determined to despatch the business themselves. Armed with clubs, maces and other weapons they marched in martial array to the hermitage of Kāsyapa. Kāsyapa invoked the goddess Prither, and desired her to show her powers against these Brāhmans. She rooted up a stout palm tree, harled it at the Brāhmans and crushed them to death.”)
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মালিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১০. জানা, ড. রাধারমণ, পালিভাষা সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১১০
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মালিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
১২. তাদেব, পৃ. ৭১
১৩. তদেব, পৃ. ৭১
১৪. তদেব, পৃ. ৭১
১৫. ঘটক, কল্যাণী শঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০০, পৃ. ৩১৮
১৬. সিংহ, বিবেক, রবীন্দ্র মননে মালিনী, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১১, পৃ-৪৪
(“ ‘মালিনী’ নাটকে নবধর্ম ও আর্যধর্মের দ্বন্দ্ব-বিরোধ বাহ্যত মালিনী ও ক্ষেমংকরকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও, প্রকৃতপক্ষে এ দ্বন্দ্বের চালকের আসনে মালিনী ছিল না, ছিল সুপ্রিয়। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সুপ্রিয়র সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংঘাতে এ দ্বন্দ্বের সূচনা; চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমাংশে সুপ্রিয় নিজে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছে, পরে ক্ষেমংকরের সঙ্গে সে ধর্মদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবশেষে তার আত্মবিসর্জনেই এ দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। ‘মালিনী’ নাটকে তাই নবধর্ম ও আর্যধর্মের যে দ্বন্দ্ব, তার দুই মেরু মালিনী ও ক্ষেমংকর হলেও এ ধর্মদ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থ শক্তি সুপ্রিয়।”)