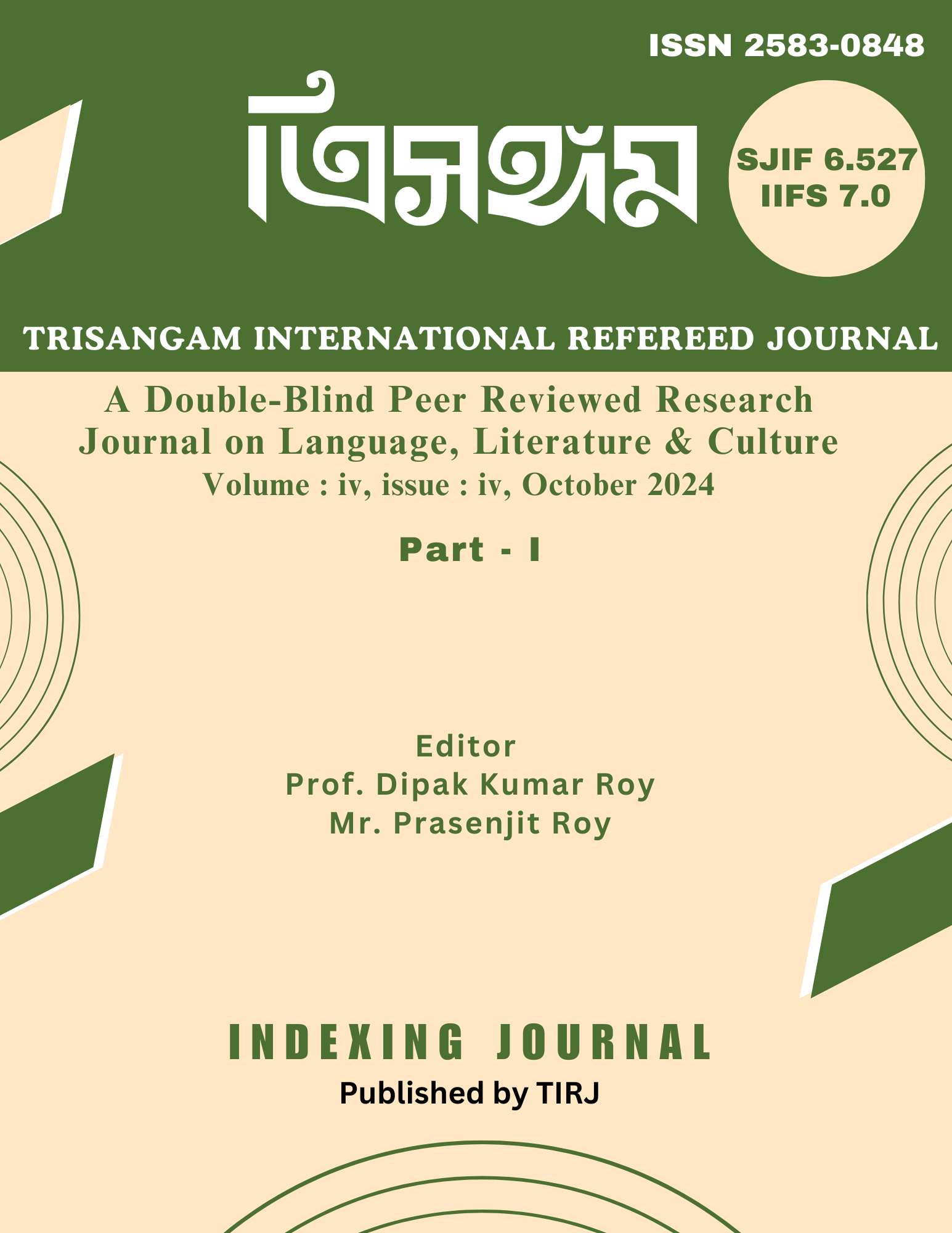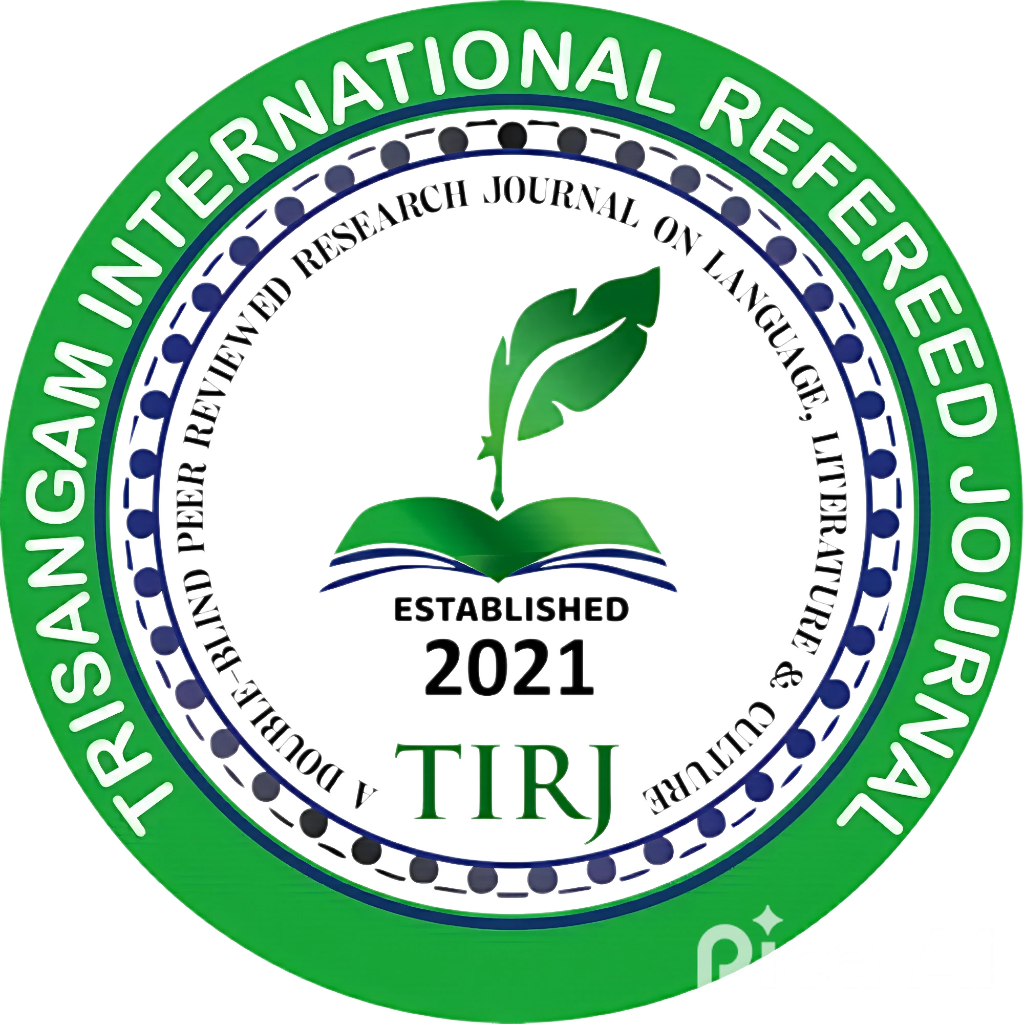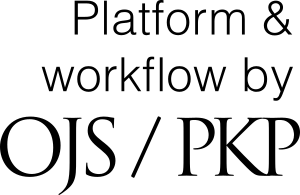Ramayana: Valmiki and Kamban/ রামায়ণ : বাল্মীকি এবং কম্বন
Keywords:
- Ancient Literature,
- Culture,
- Adaptation,
- Translation
Abstract
If we observe and review the history of world literature, it can be seen that all the works of literaturethat havebeen written in different countries of the world throughout the ages have not disappeared in thewomb of time. Rather, the eternal message of this literature has been transmitted from ancestors tofuture generations. 'Ramayana' written by Valmiki is such a complete piece of literature. The 'Ramayana' texthas an indelible impact on the Indian culture, one that no other book in this world can match. The'Ramayana' by Valmiki shaped Indian literature and research. In Bengaliliterature, KrittivasOjha's 'SriramPanchali' and Chandravati's 'Chandravati Ramayana'; Hindi literature TulsiDas's 'Ramacharitmanas' and Vishnudas's 'Bhasa-Valmiki Ramayana'; andBalaramDas's 'Ramayana' in Oriya. An adaptation of the Ramayana into the Gujarati language started in the fifteenth century and was completed by Giridharin the eighteenth century. Eknath wrote 'Bhavartha Ramayana' in Marathi in the 16th century, followed by 'Arya Ramayana' by Morapanthin the 18th century. In Telugu,'Ranganath Ramayana' was written by Buddha Reddy in the 13th century followed by 'Bhaskar Ramayana' in the 16th century, by a woman named Mollah. More recently, the poet Vishwanath Satyanarayan wrote 'Shrimad Ramayana Kalpabrikshasu'. Theadaptation of the Ramayana into the Malayalam language began in the 13th century with the poem 'Ramacharitram'. Later, the poet Kannasha Panikkar wrote the 'Kannasha-Ramayana' in the 5th centuryand Akhyapillai wrote the 'Ramakathapattu' around the same time. Kannada poet Kumar Valmiki (Narharir) wrote 'Torbeya Ramayana' in the 15th to 16th century. 'Kandali Ramayana' was written by MadhavKandali in the Assamese language in the 16th century. Nevertheless, Eduocchhan's 'Adhyatramayana' was the most popular version. Each translation is not entirely original, but also influenced by regional Ramakatha folklore. Besides, Professor V.V. Raghaban's Ramayana research book 'Studies on Ramayan' and Assamesefiction writer MamoniRaisomGoswami's books on 'Ramayana from Ganga to Brahmaputra' havefurther strengthened research on the literary origins of the epic. Its influence can also be seen in ancient Indianliterature Tamil. Although the Tamil poet Kamban takes the story from Valmiki, his 'Kamba-Ramayana' or 'Ramabhataram' stands out in its quality.
Downloads
References
১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, ভারত-সংস্কৃতি, সপ্তম মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা, ১৪১২, পৃ. ৩১-৩২
(এই ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্তর-ভারত’ প্রবন্ধে বলেছেন— “ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের মূলমন্ত্র ছিল, সকল প্রকার চিন্তা ও চর্য্যার সমন্বয় —একটি বিশিষ্ট বা শাস্ত্রানুসারী অথবা বিশেষ-সংঘ- নিয়ন্ত্রিত মতবাদের দ্বারা আর সমস্ত চিন্তা ও চর্য্যার দূরীকরণ, অপসারণ, অবনমন বা বিনাশ নহে। এই জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির কৃতিত্ব কেবল একটি বিশিষ্ট পার্থিব সভ্যতা বা সভ্য ও সমাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠাতেই নিবদ্ধ ছিল না। অবশ্য, ভারতীয় সংস্কৃতি তাহার নিজের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট আদর্শ ও তাবরাজি অন্য জাতির লোকেদের সমক্ষে আনিয়া দিয়াছিল।”)
২. ক. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, ১৪১৫, কলকাতা, পৃ. ৯
(‘রামায়ণ’-এর বিশেষত্ব সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— “রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশ-জয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধীপক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্যমাত্র: পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যাক্তি বিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।”)
খ. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, রামায়ণ ও মহাভারত, চতুর্থ মুদ্রণ, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩
(এই কাব্যের (রামায়ণ) বিশেষত্বের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রখ্যাত রামায়াণবিদ্ V. Raghaban-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন— “১৯৭৫ জানুয়ারিতে নয়া দিল্লিতে ইউনেস্কোর আয়োজনায় আন্তর্জাতিক রামায়ণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়; সম্ভবত এটি ছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিক রামায়ণ সামবেশ। রামায়ণের বহুশ্রুত পণ্ডিত প্রায়ত ভি. রাঘবনকে ওরই মধ্যে একদিন প্রশ্ন করি, ‘এতগুলি আন্তর্জাতিক রামায়ণ সভা হল, মাহাভারতকে কেন্দ্র করে কখনো কোনো সভা হয় না কেন?’ প্রথমটা উনি এমনভাবে তাকালেন যেন রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের তুলনাই সঙ্গত নয়। পরে নানা যুক্তির মধ্যে বারেবারে বললেন, রামায়ণ হল ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য, একে ঘিরেই ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কথাটা বহুলাংশে সত্য। কিন্তু সেই তখন থেকেই যে-চিন্তাটা অস্থির করে তুলছে তা হলঃ কেন এমন হল? নিজের বোধে ধরা পড়ে মহাভারত সর্বাংশে শ্রেয়স্তর মহাকাব্য, তবু অধ্যাপক রাঘবনের কথাটাও ত সত্য; আজ যাকে ভারতীয় সভ্যতা বলি তার কেন্দ্রে রামায়ণই, মহাভারত নয়।”)
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, দ্বিতীয় মুদ্রণ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১১৫
(কবি বাল্মীকি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ‘কবিজীবনী’ প্রবন্ধে বলেছেন— “আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য তিরকৌতুহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বাল্মীকির পাঠকগণ বাল্মীকির কাব্য হইতে যে জীবন চরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন তাহা বাল্মীকির প্রকৃত জীবন অপেক্ষা অধিক সত্য।”)
৪. দাশ, শিশিরকুমার, ভারত সাহিত্য কথা, প্রথম প্রকাশ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৮০
৫. চক্রবর্তী, তনিমা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাংলার লোক ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ঘ
৬. রায়, অলোক, সরকার, পবিত্র, ঘোষ, অভ্র, (সম্পাদনা), দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য, সাহিত্য একাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০০৭, পৃ. ১৫৩
(ভারতীয় সাহিত্যে ‘রামায়ণ’-এর চর্চা সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধে বলেছেন— “বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ ছাড়া, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু ছোট-বড়ো কাব্য-নাটকাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল; এবং প্রাচীন ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়, যথা পালি ও বিভিন্ন প্রাকৃতে রামায়ণকথা নানাভাবে মিলে। রামায়ণ জৈনদের মধ্যেও বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল, এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃতে জৈন রামায়ণ আছে। ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে, উত্তরভারতের আর্য ভাষার মতই রামায়ণের বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। তামিল ভাষায় মহাকবি কম্বন্ রচিত রামায়ণ তামিল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তেলুগু, কন্নড় ও মালায়ালম্ ভাষায় রামায়ণ আখ্যান লইয়া বহু কাব্য ও নাটক আছে। বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়ে রামকথা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হইতেছে-রামায়ণাশ্রয়ী কোনো-না-কোনো মহাকাব্য। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহৃদয় সাহিত্য রসিক ব্যক্তিগণের চেষ্টায় রামায়ণের একাধিক অনুবাদ বা রূপান্তর ফরাসি ভাষাতেও হইয়াছে।”)
৭. দাশ, শিশিরকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০
(কম্বনের ‘রামায়ণ’ প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে শিশিরকুমার দাশ বলোছেন— “তামিল ভাষায় রামায়ণ লেখা হয়েছিল দশম-একাদশ শতাব্দীতে। রামায়ণ কাহিনী অবশ্য তার বহু শতাব্দী আগে থেকেই তামিলনাড়ুতে প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্বন্-রচিত ‘রামাবতার কাব্যম্’ (‘কম্ব-রামায়ণ’ নামেই বিখ্যাত) তামিল সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। অনেকেই মনে করেন রামভক্তির সূচনাও দক্ষিণ ভারতে, যদিও উত্তর ভারতের মতো কোনো রামসম্প্রদায় সেখানে ছিল না। কম্বনের কাব্যে স্পষ্ট লক্ষ করা যায় বাল্মীকির মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্রের দেবায়ন। কিন্তু কবির ভক্তি সত্তা রামচন্দ্রের মানবমহিমাকে কোথাও অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আবৃত করে দেয় নি। বাল্মীকির রামায়ণের রামের মিথিলা প্রবেশ বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত। কম্বন সেখানে রচনা করেছেন এক অসামান্য মুহূর্তঃ রাম-সীতার মিলন —
‘মিথিলা নগরী
রত্নখচিত পতকা উড়িয়ে দিয়ে
দু-হাতে বাড়িয়ে অযোধ্যার রাজকুমারকে আহ্বান করল
‘এসো, এসো
আমাদের এখানে আছেন লক্ষ্মী
আমাদের বহু তপস্যার ফলে
তিনি কমলালয় ত্যাগ করে জন্ম নিয়েছেন এখানে,
হে কমলাক্ষ প্রভু, তুমিও এখানে পদার্পণ করো।’
কম্বন বাল্মীকির অনুসরণ করেই ক্ষান্ত নন, তিনি নিজের কল্পনায় তৈরি করেছেন নতুন নতুন মুহূর্ত, সৃষ্টি করছেন নতুন সৌন্দর্য। রামসীতার মিলন দৃশ্য এঁকেছেন কম্বন প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁদের ভালোবাসা। সখী-পরিবৃতা সীতা দাঁড়িয়ে রয়েছেন অলিন্দে। দূরে আসছেন রামচন্দ্র। তাঁদের চার চোখের মিলন হল। একে যেন অন্যকে গ্রাস করল। সীতা স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন, তাকিয়ে রইলেন অপলক চোখে, আর মিলে এক হয়ে গেলেন দুজনে।”)
৮. মহারাজন্, এস., কম্বন (অনুবাদ : কৃষ্ণমূর্তি, সুব্রমণিয়ন্), প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬
৯. ভৌমিক, তাপস (সম্পাদনা), রামায়ণ চর্চা ভারতে বহির্ভারতে, প্রথম প্রকাশ, কোরক, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৩২