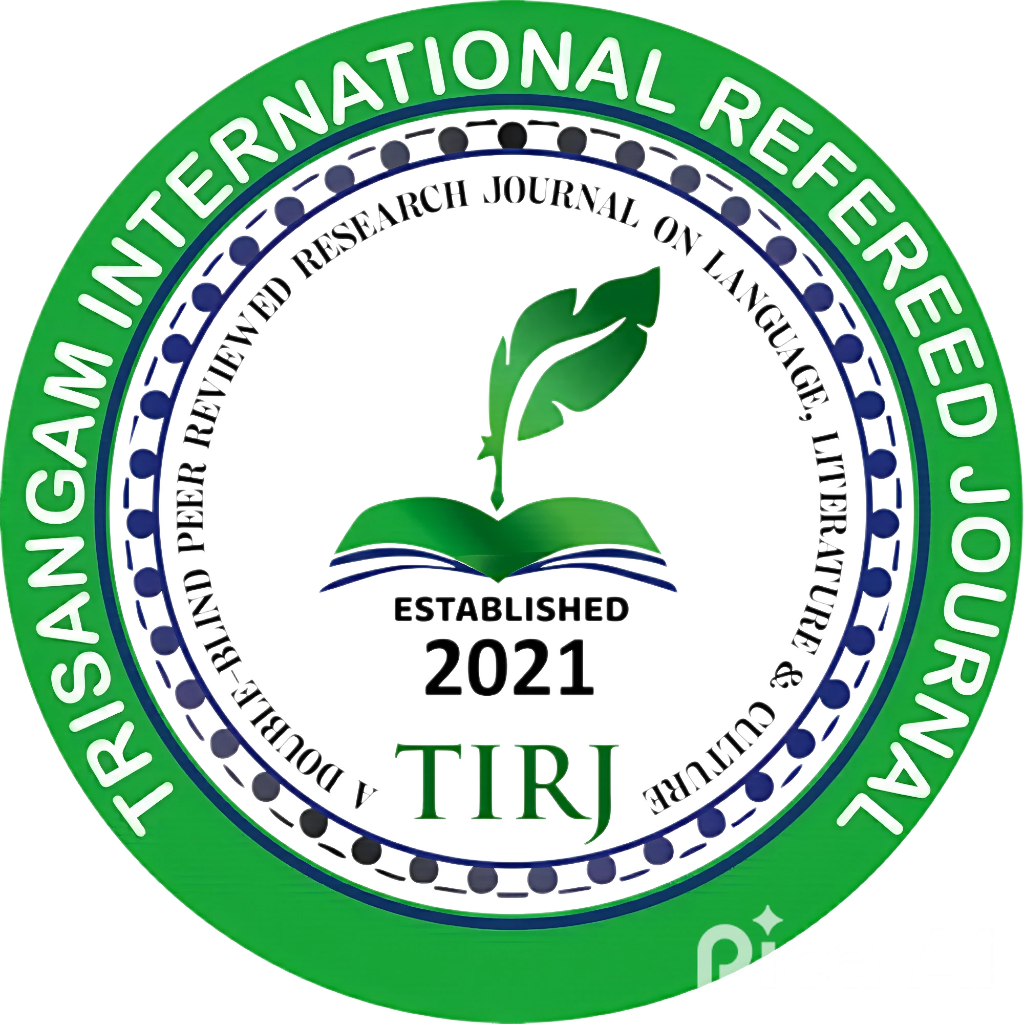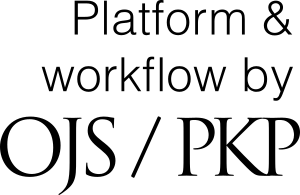Ancient Indian Tales: 'Baital Pachchisi' and 'Betal Panchavinshati'/ প্রাচীন ভারতীয় উপাখ্যান : ‘বৈতাল পচ্চীসী’ এবং ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’
Keywords:
- Indian and Western trend,
- Folk education,
- Cultural Transformation,
- Ethical Values
Abstract
In ancient India, anecdotes served as a primary vehicle for folk education. One of their main purposes was to educate the unlearned masses and to instill ethical values in children, preparing them to become civilized adults. Anecdotes were a pervasive form of cultural transmission, often carrying the lessons of folk education even without a formal teacher. This made them a powerful tool not just in Eastern traditions, but in Western ones as well. The 'Betal Panchavinshati' seems to have emerged from this ancient Indian tradition of anecdote writing. Its style of storytelling is influenced by the anecdotes found in the 'Vedas', 'Upanishads', 'Ramayana', 'Mahabharata', and 'Jataka Tales'. The original style, known as Baddakaha, was written in the Paishachi-Prakrit language. This style later evolved and was incorporated into the Sanskrit work 'Katha saritsagar', a section of which became widely known as the 'Betal Panchavinshati'. We can analyze the similarities and differences between two modern versions of this classic: Hindi writer Lallulal's 'Vaital Pachchisi' and Bengali writer Ishwar Chandra Vidyasagar's 'Betal Panchavinshati'. Both authors avoided the original source material, creating unique works with natural similarities. Despite their constraints, both books were written with a distinctiveness that makes their differences just as significant as their similarities.
Downloads
References
১. রায়, বিশ্বনাথ ও চক্রবর্তী, শুক্লা (নির্বাহী সম্পাদক), তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ. ৭০
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, পুনর্মুদ্রণ, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ. ২৭
সোমদেবের ‘কথাসরিৎসাগর’ এবং ক্ষেমেন্দ্রের ‘বৃহৎকথামঞ্জরী’ গ্রন্থে বেতালের আখ্যানের কথা থাকলেও মূল গল্পগুলির উৎস সম্পর্কে A.B. Keith এর ‘History of Sanskrit Literature’ (1941) গ্রন্থে উল্লেখ করে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—
“শিবদাস ভট্ট, জম্ভল দত্ত এবং বল্লভদাসের নামে ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’র নানা সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গেছে। কেউ কেউ বলেন গল্পগুলি নাকি পূর্বে ছন্দেই লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে বল্লভদাসের গল্পগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত।”
৩. Tarkalnnkar, Harish Chandra, The Bytal-Pacheesee or The Twenty-five. Tales of the Demon (Vidyasagara's Edition), Lees, W. Nassan, 1858 (দ্র. তদেব, পৃ. ২৭)
এখনো পর্যন্ত ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’র তিনটি নির্ভর যোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে জীবনানন্দ, বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় জন্তল দত্তের বেতাল নাগরী অক্ষরে ছাপা হয়। বেতালের এটিই হচ্ছে কলকাতায় প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ। এরপরে লাইপজিগ ১৯১৫ সালে শিবদাস ভট্টের মূল সংস্কৃত বেতাল জার্মান টীকাসহ প্রকাশিত হয় ‘Die Vetala Pancauimsatika’ নামে। ১৯৩৪ সালে American Oriental Series-এর চতুর্থ খণ্ডে জম্ভল দত্তের বেতাল প্রকাশিত হয়।
৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে রাজা জয়সিংহের আদেশে সুরত কবীশ্বর ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’র ব্রজভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ বিল প্রাইস্টের অনুরোধে কলেজের জন্য মুন্সী মুজাহার আলি খাঁ যিনি ‘বিল’ নামে হিন্দুস্থানী বা হিন্দি সাহিত্যে পরিচিত এবং লল্লুলাল কব্ ব্রজ ভাষা থেকে হিন্দি ভাষায় ১৮০৫ সালে ‘বৈতাল পচ্চীসী’ নামে এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় এই গ্রন্থটি ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয় এবং নতুন সংস্করণরূপে ১৮৫৮ সালে হরিশ্চন্দ্র তর্কালংকারের দ্বারা বিদ্যাসাগরের সংস্করণে পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।
৫। (ক) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
বিদ্যাসাগরের ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ অনুবাদ সম্পর্কে জানা যায়—
“ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ (সেক্রেটারি) জি. টি. মার্শেলের নির্দেশে বিদ্যাসাগর ‘বৈতাল পচ্চীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন’ (দ্বিতীয় সংস্করণ বেতালের বিজ্ঞাপন) করে অনুবাদ করেন এবং নাম দেন ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’। এর প্রথম থেকে নবম সংস্করণ পর্যন্ত তিনি বিরাম চিহ্ন হিসেবে শুধু দাঁড়ি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দশম সংস্করণ (১৯৩৩ সংবৎ-১৮৭৭ খ্রিঃ অঃ) থেকে ইংরেজী রীতির কমা-সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছিল। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ না করে তিনি হিন্দুস্থানী ‘বৈতাল পচ্চীসী’ থেকে কেন অনুবাদ করলেন তার কারণ দুজ্ঞেয় নয়। প্রথমবার ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজ সেরেস্তাদারের (অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিত) পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে তাঁকে বিদেশি ছাত্রদের বাংলা পড়াতে হত, বাংলা ও হিন্দিতে লেখা উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে হত। কার্যানুরোধে তাঁকে বেশ ভালো করে ইংরেজী ও হিন্দী শিখতে হয়েছিল। একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত প্রতিদিন তাঁকে হিন্দী শেখাতেন। এভাবে তিনি অল্পকালের মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানী ভাষায় বিশেষ অধিকার অর্জন করেন। হিন্দু ভাষা-জ্ঞান তাঁর কিরকম আয়ত্তে এসেছে তার পরীক্ষা করবার জন্যই বোধহয় তিনি হিন্দী ‘বৈতাল পচ্চীসী’ অবলম্বনে ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ রচনা করেন। অবশ্য এর কিছু কিছু উগ্র আদিরসের বর্ণনা (যা মূল সংস্কৃতেও ছিল) তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে ত্যাগ করেছিলেন,”
(খ) মিত্র, ইন্দ্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৩২
এই রচনা সম্পর্কে উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন— “বেতালপঞ্চবিংশতি নামে যে হিন্দি বই আছে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থখানি উহার নামমাত্র অনুবাদ। হিন্দিতে তিনি কেবল কঙ্কালখানি পাইয়াছিলেন; রক্ত মাংস ইত্যাদি সকলই তিনি আপনা হইতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন।”
৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৯৫
রবীন্দ্রনাথ ‘সাধনা’ পত্রিকার ভাদ্র (১৩০২) সংখ্যায় বলেছেন—
“বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।... বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন-এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্রে আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন-কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।... বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলির নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা— উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃজনক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া য়ায়।”
৭. রায়, বিশ্বনাথ ও চক্রবর্তী, শুক্লা (নির্বাহী সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১